নকল ওষুধ, অসাধুতার চিত্র প্রায় একই
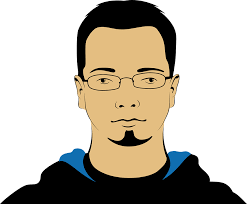
- আপডেট টাইম : মঙ্গলবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২২

রিন্টু আনোয়ার:
স্বাস্থ্যই সব সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, ডাক্তার ও ওষুধ। আর ওষুধই অসুস্থতার একমাত্র নিয়ামক। বর্তমানে বাংলাদেশে ওষুধ শিল্প অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক ভালো সময় পার করছে। দেশের প্রয়োজনীয় সব ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন করতে সমর্থ। সূত্র মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫৭টি কারখানায় প্রায় ২৪ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন হচ্ছে। দেশীয় কোম্পানিগুলো বছরে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার ওষুধ ও কাঁচামাল তৈরি করছে। এতে দুই লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ ওষুধের চাহিদা পূরণ করছে দেশীয় কোম্পানিগুলো। তা ছাড়াও দেশের অর্থনীতিতে রাখছে বড় ভূমিকা। বাংলাদেশের উৎপাদিত ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ১৪৫টি দেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলাদেশের উৎপাদিত ওষুধের চাহিদা ও ব্যবহার বিশ্ববাজারে বেড়েই চলেছে।
এত সব সুখবরের মধ্যে খারাপ খবর হচ্ছে, দেশীয় বাজারে উৎপাদিত হচ্ছে প্রচুর ভেজাল ও নকল ওষুধ, যার ফলে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে ওষুধ শিল্প ও চিকিৎসাব্যবস্থা। ফলে ভেজাল ও নকল ওষুধ এই শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে এক বিরাট অশনি সঙ্কেত।
দিন দিন বেড়েই চলেছে নকল ও ভেজাল ওষুধের রমরমা ব্যবসায়। একই সাথে বাড়ছে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা।
মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ডাক্তারের ফি ও টেস্টের (রোগ নির্ণয়) খরচের অঙ্কে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যান কম, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সরাসরি চলে যান ওষুধের দোকানে। দোকান থেকে রোগের বিবরণ দিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে এসে খাচ্ছেন অহরহ।
শুধু তা-ই নয়, কেনার সময়েও খোঁজেন কম দামি ওষুধ। আর তাই এরই সুযোগ নিচ্ছে ভেজাল ওষুধ প্রস্তুতকারীরা।
যখন ওষুধ সেবন করা হয়, তখন বোঝার উপায় থাকে না ওষুধটি নকল নাকি আসল। ফলে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান।
অবশ্য ক্লিনিক-হাসপাতালই যেখানে বিনা লাইসেন্সে চলছে, সেখানে ওষুধ দোকানের লাইসেন্স না থাকলে কি-ই বা যায়-আসে! এমন একটি ভাব ভর করেছে কারো কারো মাঝে। করোনার মোক্ষম মৌসুম দৃষ্টে রাতারাতি শহর-বন্দর-জনপদের আনাচে-কানাচে গজিয়েছে বহু ফার্মেসি। করোনা দুর্যোগ সময়ে বিভিন্ন ওষুধের চাহিদা কয়েকগুণ বাড়ায় এসব দোকানের ব্যবসায় বেশ জমেছে। নকল, ভেজাল, মানহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধও নিমিষে চালিয়ে দেয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে দেদার।
বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিবন্ধনহীন ফার্মেসির সংখ্যা দেড় লাখ বলে প্রচারিত। আবার বৈধ দোকানের সংখ্যাও এমনই। সংখ্যা যা-ই হোক বিশাল হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফার্মেসি খুলতে কিছু নিয়ম রয়েছে। পাইকারি-খুচরা দুই ধরনের লাইসেন্স রয়েছে। তা ড্রাগ লাইসেন্স নামেই বেশি পরিচিত। খুচরা ওষুধ বিক্রির জন্য দুই ক্যাটাগরিতে এ লাইসেন্স দেয় অধিদফতর। একটি মডেল ফার্মেসির, আরেকটি মেডিসিন শপের। মডেল ফার্মেসির জন্য প্রয়োজন হয় ৩০০ ফুটের একটি দোকান, পৌরসভার ভেতরে হলে দুই হাজার ৫০০ টাকা এবং বাইরে হলে এক হাজার ৫০০ টাকা। সাথে দিতে হয় ১৫ শতাংশ ভ্যাট। এর বাইরে আরো কিছু নিয়ম রয়েছে। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি, মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, মালিকের ব্যাংক সচ্ছলতার সনদ, ফার্মেসিতে নিয়োজিত গ্র্যাজুয়েট বা এ গ্রেড ফার্মাসিস্টের রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, ফার্মাসিস্টের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ফার্মাসিস্টের অঙ্গীকারনামা, দোকান ভাড়ার চুক্তিনামা প্রভৃতি।
করোনা মহামারীকে পুঁজি করে ঢাকাসহ সারা দেশের অলিগলিতে গড়ে উঠেছে নতুন অসংখ্য ওষুধের দোকান। এগুলোর বেশির ভাগই অবৈধ। কিছু বৈধও আছে। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাগেযোগে করলে লাইসেন্স পেতে বেশি সমস্যা হয় না। সেখানকার লোকেরাই কন্ট্রাক্টে কাগজপত্র সব তৈরি করে দেন। বেকার-আধাবেকার অনেকেই ঝুঁঁকেছেন এ ব্যবসায়। মুদি দোকানদার, সেলুন বা লন্ড্রি মালিকরাও ওষুধের সাইড বিজনেস খুলে বসেছেন। ওষুধ কোম্পানিগুলোর অতি ব্যবসায়িক মনোভাব এবং জনসাধারণের অসচেতনতার কারণে ফার্মেসিগুলো বেশ চলছে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবের নির্দেশে দেশের সব জেলার ড্রাগ সুপার, সিভিল সার্জন, উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজ নিজ এলাকার ওষুধের দোকানের তথ্য জানাতে বলা হয়েছিল। এর কোনো ফলোআপ তথ্য নেই।
একটি খুচরা বা পাইকারি দোকানের ড্রাগ লাইসেন্স নেয়ার পর প্রতি দুই বছর অন্তর নবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন না হলে বিলম্ব ফি দিয়ে নবায়নের সুযোগ আছে। কিন্তু বছরের পর বছর পার হলেও লাইসেন্স নবায়ন করছেন না অনেক ব্যবসায়ী। এতে সমস্যা হচ্ছে না। যেখানে লাইসেন্সই লাগছে না, সেখানে তাদের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের গরজই হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্যের মতো মানুষের ওষুধের প্রয়োজন হয়। শুধু বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর ১৪০টি দেশে ওষুধ রফতানি হয়। বাংলাদেশে যে ওষুধের চাহিদা তার ৯৫ শতাংশ বাংলাদেশেই তৈরি হয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই যে কেউ ফার্মেসি ব্যবসা শুরু করতে পারবেন না। ওষুধ তিনিই বিক্রি করতে পারবেন, যার ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং ও ড্রাগ লাইসেন্স আছে। ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ওষুধের ব্যবসা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং আইনগতভাবে এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আর ওষুধ ব্যবসার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই ড্রাগ লাইসেন্সটি ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকারের ‘ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর’। তিনটি ক্যাটাগরিতে ড্রাগ লাইসেন্সের রেজিস্ট্রেশন হয়। গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টরা ‘এ’ ক্যাটাগরির, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টরা ‘বি’ ক্যাটাগরির ও শর্ট কোর্স সম্পন্নকারীরা ‘সি’ ক্যাটাগরির লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। ‘বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল’ থেকে ‘সি’ ক্যাটাগরির ফার্মাসিস্ট হিসেবে ড্রাগ লাইসেন্স অর্জন করতে হলে বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির তত্ত্বাবধানে দুই মাসের ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড সমিতির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। বাংলাদেশের সব জেলায় কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির আওতায় দুই মাসের শর্ট কোর্সটি করানো হয়। এ সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকার মিটফোর্ডে। এসএসসি পাস করে যে কেউ এ কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। সর্বমোট ৪০টি ক্লাস করানো হয়। কিন্তু বাঁকা পথে গেলে কিছুই লাগছে না।
পুরনো ফার্মেসি মালিকদের অনেকেই মুনাফার কারসাজিতে অভিজ্ঞ। সে কারণে সাধারণ মানুষের ‘পকেট কাটার’ নানা কৌশল অবলম্বন করে লাভও করতে পারছেন বেশি। অন্য দিকে লোকসানের কারণে ওষুধের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে এমন নজির খুব কম; বরং দেশে নিয়মিত বাড়ছে ওষুধের দোকান। ওষুধ প্রশাসনের কার্যকর তদারকির অভাবে রাজধানীসহ সারা দেশে লাইসেন্স ছাড়াই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ফার্মেসি। ওষুধ বিক্রির পর টাকা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেকটা অল্প পুঁজিতেও ব্যবসায় করতে পারছে ফার্মেসিগুলো। ভোক্তাদের প্রয়োজন আর চাহিদা বুঝে ফার্মেসি মালিকদের অনেকে প্রায় নিয়মিতই ওষুধের অযৌক্তিক দাম আদায় করছেন। বিশেষ করে মৌসুমি অসুখ-বিসুখে যেসব ওষুধের চাহিদা বেশি সেগুলোর দাম দোকানে দোকানে তারতম্য হয়। হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ব্যবহৃত বিদেশী উচ্চমূল্যের ওষুধের দাম রাখা হয় যথেচ্ছ হারে। কোনো কোনো ওষুধের দাম আমদানি মূল্যের তিন-চারগুণ। শুষ্ক মৌসুমে অ্যাজমার প্রকোপ বেড়ে গেলে ইনহেলারের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে বেশি দাম রাখা হয়।
এ দিকে কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় ওষুধ বিপণন এখন ‘মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ’ নির্ভর হয়ে পড়েছে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা দোকানিকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে নিজেদের ওষুধ বাজারজাত করতে তৎপর থাকে। ফলে বাকিতে ওষুধ রেখে বিক্রি করে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা থাকছে। এ জন্য কম পুঁজিতেও ওষুধের ব্যবসা জমিয়ে তোলা যায়। এর বাইরে স্যাম্পল ওষুধের ব্যবসাও চলছে। উৎপাদনকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের বিনামূল্যে দেয়া এসব ওষুধ কেনাবেচা নিষিদ্ধ। কিন্তু চিকিৎসকরা টাকার বিনিময়ে এসব ওষুধ ফার্মেসিতে বিক্রি করে দেন। এসব কারণে সারা দেশে ফার্মেসির সংখ্যা বাড়ছে। সামনে আরো বাড়ার লক্ষণ স্পষ্ট। এর লাগাম টানার কিছু চেষ্টা যে হচ্ছে না এমনও নয়। সম্প্রতি ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান বেড়েছে। তারা হানা দিচ্ছে বিভিন্ন ফার্মেসিতে।
কোথাও কোথাও নিবন্ধন থাকা ফার্মেসিতেও মিলছে ভেজাল মানহীন ওষুধ। ওষুধগুলোর গায়ে নেই উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, কোম্পানির নাম, লোগো, রেজিস্ট্রেশন নম্বর। রয়েছে বিক্রি নিষিদ্ধ স্যাম্পল ও অনুমোদনহীন ওষুধ। ঢাকাসহ সারা দেশে ফার্মেসিগুলোর অনিয়ম-অসাধুতার চিত্র প্রায় একই। অথচ অসাধুতা-অনৈতিকতা না করলেও ব্যবসাটি সাফল্যের সাথেই করা যায়। এর জন্য অনেক পুঁজি বা অনেক যোগ্যতার দরকার পড়ে না। সামান্য একটু দৌড়াদৌড়ি করলেই ব্যবসাটি শুরু করা যায়। বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের অধীনে তিন মাসের ফার্মাসিস্ট কোর্সটি করা কঠিন নয়। এর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে এসএসসি পাস। কোর্স শেষ করার পর একটি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যেটির মাধ্যমে কোনো একজন ড্রাগ লাইসেন্সের মালিকের রেফারেন্স নিয়ে বৈধভাবেই ব্যবসাটির সূচনা করা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঁকাপথের মোহ বেশি। লাভের জন্য নকল বা মেয়াদহীন ওষুধ বিক্রির দরকার পড়ে না। আসল ওষুধেও যথেষ্ট লাভ। ওষুধ ব্যবসায় মুনাফা নিয়ে নানা কথা রয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন রকম হিসাব কষেন ব্যবসায়ীরা। নতুন ব্যবসায়ীদের সাধারণত গড় লাভ থাকে ১০-১২ শতাংশ, আর পুরনোদের ৩০-৩৫ শতাংশ। অদ্ভুত এই হিসাব ওষুধ ব্যবসায়ীদের নিজেদের।
কমবেশি বিশ্বের আরো কিছু দেশেই নকল ও ভেজাল ওষুধ বিক্রি হয়। পাকিস্তান, ভারত, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে নকল ওষুধ উৎপাদনকারী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। করোনায় নানা ওষুধের চাহিদা বুঝে তা আরো বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হাতেগোনা কিছু ওষুধ বিক্রেতা ও কিছু প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় এনে জরিমানা করে ছেড়ে দিচ্ছে, আবার কিছু মামলাও হচ্ছে। কিন্তু প্রতিকার নেই।
সর্বোপরি ভেজাল, নকল ওষুধের ব্যাপারে সরকারের আরো সজাগ হওয়ার দরকার রয়েছে। পাশাপাশি সচেতন হতে হবে মানুষকেও। চীনে ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশালে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। বাংলাদেশে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা জরুরি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে ১৯৪০ সালের ড্রাগ অ্যাক্ট বা ওষুধ আইন বলবৎ আছে। এ আইনের আওতায় যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা খুবই নগণ্য। অপরাধের চেয়ে শাস্তির মাত্রা এতই কম যে, তাতে অপরাধ ও অপরাধীর ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না। নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি করার মাধ্যমে মানুষ হত্যার শাস্তি এক বা দুই লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক, দুই বা তিন মাস জেল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর তাই, মানুষ নকল, ভেজাল ওষুধ চিনতে শুরু করলে ভেজাল কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় দমতে বাধ্য।
লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট



















