খাওয়ার জন্য বাঁচি, না বাঁচার জন্য খাই
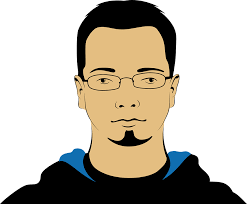
- আপডেট টাইম : শুক্রবার, ১২ নভেম্বর, ২০২১

জয়নুল আবেদীন :
সোস্যাল মিডিয়ায় বাঙালির ভাত খাওয়া নিয়ে তোলপাড় চলছিল। তোলপাড় থেকে ‘আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি, না বাঁচার জন্য খাই?’ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। এক হাউজিং কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রতি শনিবার যাই কোম্পানির অফিসে। অফিসের উল্টো দিকে একটি অভিজাত হোটেল। হোটেলের খাদ্যের মান ও উচ্চমূল্য সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে। একদিন লাঞ্চ করার জন্য প্রবেশ করি। টপফ্লোরে ডাইনিং হল। লিফটে উঠে ডাইনিংয়ে বসে খাবারের মূল্যতালিকা হাতে নিয়ে ভড়কে যাই। কমদামের মধ্যে প্লেইন রাইস প্রতি প্লেট ১১০, সবজি ১০০ টাকা এবং ডাল ১২০ টাকা। এই তিন প্রকারের খাবার অর্ডার দিয়ে মিনিট ত্রিশেক অপেক্ষার পর গরম খাবার আসে। গরম খাবারের বাষ্পের সাথে যে ঘ্রাণ ভেসে আসছিল তা ভুলবার মতো নয়। মুখে তুলে বুঝতে পারি, স্বাদ কারে কয়! যেমন সুস্বাদু ভাত, তেমন মজা সবজি আর সেরকম তৃপ্তিকর ডাল। খাওয়া শেষ করে বকশিশ দেয়ার কথা বলে বাবুর্চির কাছে জানতে চাই,
– এই চাল কোন দোকান থেকে কেনেন?
– কেন?
– আজই আমি কিনে নিয়ে যাবো।
– কোনো দোকানেই আপনি এ চাল পাবেন না। বরিশালের কিছু কৃষক এই ধানের চাষ করেন। ঢাকার কয়েকটা হোটেল অগ্রিম টাকা দিয়ে এই ধানের চাষ করানো হয়। আমাদের আদেশের বাইরে এ চাল বিক্রি করতে পারবে না।
আমার বাবাও ছিলেন একজন কৃষক। ভাত খাওয়ার জন্য বাবার একটা বড় পিতলের থালা ছিল। থালা ছাড়া বাবার ভাত খেয়ে মন ভরত না। বাবার ফসলের জমিতে মুনি-কামলাদের (দিনমজুর) খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে আমিও যেতাম। প্রধান তরকারি খাটাই (কাঁচা আম, গুঁড়া চিংড়ি ও মিষ্টি আলুসহযোগে এক প্রকার পাতলা তরকারি) নিতাম অ্যালুমিনিয়ামের কলসি ভরে। চার-পাঁচ কেজি চালের ভাত ৮-১০ জন মজুর অনায়াসে খেয়ে শেষ করত। খেয়েই বলত, ‘চাচী বলো, জেঠী বলো, মায়ের মতোন নয়, পিঠা বলো, চিঁড়া বলো, ভাতের মতোন নয়’। আবহমানকাল থেকে এ দেশের মানুষ ভাতকে মায়ের সাথে তুলনা করে আসছে। কারণ অনুক‚ল আবহাওয়াসহ নদীবহুল বাঙ্গালা অঞ্চল কৃষিকাজের অনুক‚লে। তাই সভ্যতার উন্মেষ থেকে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি গড়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক। কৃষকের প্রধান ফসল ধান। বর্ষা, হেমন্ত ও শীত এই তিন কাল অনুসারে ধানকে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আউশ শব্দের অভিধানিক অর্থ আশু বা শীঘ্র। কৃষকদের দেখতাম, চৈত্র মাসের দিকে অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে আমন ধানের সাথে আউশ ধানের বীজ বপন করতেন। আষাঢ় মাসের দিকে পেকে গেলে কোমর বা বুকজলে নেমে বাছাই করে আউশ ধান তুলে আনতেন। কয়েক প্রকার আউশ ধানের মধ্যে কুচকুচে কালো ধানটির নাম ‘হাইট্টা’। আমাদের এলাকা থেকে হাইট্টা ধান হারিয়ে গেছে কয়েক যুগ আগে। হাইট্টা ধান এখন আর দেখা যায় না। ডিসেম্বর ২০১৬ সালে নিঝুমদ্বীপ গিয়েছিলাম। ছিলাম নামারবাজার নিঝুম রিসোর্টে। নামারবাজার এলাকায় হাইট্টা ধান দেখতে পেয়েছি। অনেক দিন পর কুচকুচে কালো রঙের হাইট্টা শুকাতে দেখেই মনে পড়ে গেল, আমন ধানের সাথে বাবাও বুনতেন হাইট্টা ধান। হাইট্টা ধানের চিঁড়া-মুড়ি বিখ্যাত বলে ছড়া ও গানে এ ধানের নাম পাওয়া যায়,
‘হাইট্টা ধানের মাইট্টা চিঁড়া গোয়াল বাড়ির দই,
সকল জামাই খাইতে বইছে; লেংড়া জামাই কই?’
আমন ধানের এক বিস্ময়কর গুণ হলো, পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায় ধানের গাছ। প্রকার ভেদে কোনো কোনো আমনের গাছ ১৪-১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। শুরু হয় অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব। কখনো কখনো আগাম বর্ষায় তলিয়ে যায় পানিতে। তারপর রয়েছে পামরিপোকার আক্রমণ। মাঠের পর মাঠ শেষ করে ফেলে। আমন ধান কাটা হয় কার্তিকের মাঝামাঝি। দীর্ঘ দিন প্রতিক‚ল অবস্থার সাথে লড়াই করে কৃষকের গোলা ভরত আমন ধানে। আমন ধানের আঞ্চলিক নাম খামা বা বাওয়া। নানা জাতের খামার মধ্যে আমাদের চর এলাকায় লালিখামা, ধলিখামা, ইজলিখামা, গাবুরা, লেঞ্জা, মুইরল ও গৌরল ধান বেশি দেখা যেত। আমাদের ছিল কৃষক পরিবার। দেখতাম, এসব ধানের বীজ বাবা নিজেই সংরক্ষণ করতেন। বিশেষ করে প্রথম ওঠানো ফসল থেকেই বাবা বীজ রাখতেন। নিচু এলাকায় ছিল আমাদের তিন খণ্ড জমি। অত্যধিক গভীরতার কারণে বোনা হতো লেঞ্জা আমন। বাড়ির লাগ দক্ষিণের জমি সবচেয়ে উঁচু। উঁচু জমিতে বুনতেন গাবুরা। আমাদের বাইন শুরু লেঞ্জা ধান দিয়ে, শেষও লেঞ্জা ধান দিয়ে। ভাত ছাড়াও মুড়ি, চিঁড়া, খৈ, পিঠা, পায়েস তৈরিতে লেঞ্জা ধানের জুড়ি নেই। রোগীর জন্য লেঞ্জা চালের জাউ উত্তম পথ্য। ভিন্ন স্বাদ ও ঈষৎ ঘ্রাণযুক্ত লেঞ্জা চালের সামগ্রী যে না খেয়েছে, তাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ভাদ্র মাসে ধানগাছ জট বাঁধতে শুরু করে। বাবা কোষা নৌকায় করে আমাকে নিয়ে ক্ষেতের আলে আলে ঘুরতেন। কখনো কখনো কোষা থামিয়ে ধানগাছের পেট টিপতেন। পেট টিপে দেখতেন, গাছের পেটে থোড় জন্মেছে কি না। শরতের শেষে আশ্বিনের ঝড়। ঈশানের কোণে কালো মেঘ জমতে শুরু করলে কিষানের মুখেও কালো মেঘ জমতে শুরু করে। নদীর পাড়ে আমাদের এক খণ্ড বড় জমি। আশ্বিনের ঝড় মাঝে মাঝেই ওই জমির ধান ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঝড়ের সময় দড়ি-কাছি ও বাঁশ-লগি নিয়ে ধান রক্ষা করতে গিয়ে বাবার কষ্টের কথা মনে হলে এখনো কষ্ট পাই। সব কষ্ট দূর হয়ে যায় নবান্নের ঘ্রাণে। নতুন ধানের নবান্ন বাঙলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। জীবনানন্দ দাশ মরে গিয়েও ভোরের কাক হয়ে এই নবান্নের ঘ্রাণ নেয়ার জন্য ফিরে আসতে চেয়েছেন,
‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে
…. হয়তো ভোরের কাক হয়ে
এই কার্তিকের নবান্নের দেশে’
নবান্নের ঘ্রাণ এখনো যেন নাকে লেগে আছে। আমন ধানের জাউ-চিঁড়াসহ ভোর হতে না হতে পিঠা বানানো শুরু। বাড়ি বাড়ি চাল তুলে শুরু হয় খোদার নামে সিন্নির আয়োজন। নদীর পাড়ে জেগে ওঠা তিন পথের মাথায় রান্না হতো ‘খোদাই শিন্নি’। কেউ দুধ কিনে আনে, কেউ ভাঙে নারিকেল। কাঁচা মাটি গর্ত করে চুলা। পাঁচ-সাতটি বড় ডেগে দুপুর থেকে শুরু রান্না। সন্ধ্যার আগেই সানকি হাতে মাটির উপর নাড়া বিছিয়ে লাইনে বসে সিন্নি খাওয়ার স্মৃতি চাইলেই কি ভুলা যায়? শুধু সিন্নি আর ভাত নয়, নবান্নের ফেনেও ছিল ঘ্রাণ। মা নতুন চালের প্রথম ভাত খেতেন ফেন দিয়ে। নতুন ফেন-ভাতের সাথে একটা পোড়া মরিচ মিলিয়ে খাওয়ার সময় আমার মুখেও কয়েক লোকমা তুলে দিতেন। আহ্ আমন ধানের চালের ভাতের কী স্বাদ! স্বাদ গ্রহণের জন্য সারাক্ষণ ‘আবদুল হাই’-এর মতো খিদে লেগেই থাকত। তখনই মনে হয়, লুৎফর রহমান রিটন ‘খিদে’ ছড়াটি লিখেছেন,
‘আবদুল হাই করে খাই খাই
এক্ষুণি খেয়ে বলে কিছু খাই নাই
… খেতে খেতে খেতে খেতে
পেট হলো ঢোল
তবু তার মুখে সেই পুরাতন বোল
কী যে অসুবিধে খালি পায় খিদে।’
১৯৬৯ সালে আমরা কয়েকজন স্কুল বোর্ডিংয়ে থেকে এসএসসির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সবাই বাড়ি থেকে চাল এনে রান্না করে খাই। আমাদের মধ্যে একজনের বাড়ি সোনারগাঁওয়ের আনন্দবাজার এলাকায়। নাম ওসমান গনি। আমাদের ভাত বাদামি রঙের; ওসমান গনির ভাত ধবধবে সাদা। চোখ যেত সাদা ভাতের দিকে। অদল-বদল করে খেতে গিয়ে ঠকার বিষয়টি দু’দিনেই টের পাই। ওসমান গনির ভাত ইরি ধানের চালের আর আমার ভাত আমন ধানের চালের। স্বাদের দিক থেকে আকাশপাতাল তফাত। ইরি ধান ঘরে আসে তিন মাসে – প্রতি একরে ফলন ৬০ থেকে ৭০ মণ আর আমন ধান আট-নয় মাসে ঘরে আসে। প্রতি একরে ফলন ২৪ থেকে ২৫ মণ। শত খোঁড়াখুঁড়ির পর ঘরে আসা চালের ভাতে যে রকম ঘ্রাণ সে রকম স্বাদ।
এ কারণেই যেখানে কৃষিপ্রধান দেশের মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচতে চায়, সেখানে শিল্পপ্রধান দেশের মানুষ বাঁচার জন্য খায়। যেমন, ‘এ দেশের মানুষ কখনো আস্তে হাঁটে না আবার জোরেও দৌড়ায় না। হাঁটে লম্বা কদমে দ্রুতচালে। বাম হাতে খাবারের ঠোঙা; ডান হাতে পাইপ লাগানো কোকের কনটেইনার। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে ট্রেন বা বাসে ওঠে। খাবারের ঠোঙা থেকে চিপস চিকেন মুখে পুরে এক দিকে চিবুচ্ছে আরেক দিকে পাইপ থেকে টেনে নিচ্ছে কোক। তাদের হাঁটা, চলা, খাওয়া ও গাড়িতে ওঠা-নামা দেখলে মনে হয় সবকিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে – যা যা করার এ মুহূর্তে করে নাও।’ (বিলেতের পথে পথে পৃষ্ঠা ১১০)
কারো বুদ্ধি-পরামর্শে নয়, বাঙালির খাওয়ার প্রবণতা কমে গেছে হাইব্রিড ও ফরমালিনে। অতি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতে গিয়ে খাদ্যের স্বাদ হারিয়ে যাচ্ছে। ধান ছাড়াও হাইব্রিড বীজ থেকে উৎপদিত শাকসবজি ও ফল-ফলাদিতে হাটবাজার সয়লাব। হাইব্রিড দ্রব্য সহজে পচে।
সংরক্ষণের জন্য মেশানো হয় ফরমালিন। হাইব্রিড নিয়েছে খাদ্যের স্বাদ আর ফরমালিন নিয়েছে ঘ্রাণ। ফরমালিন ঘ্রাণ কেড়ে নেয়া ছাড়াও হাত বাড়িয়েছে আমাদের চোখ, লিভার, কিডনি, হার্ট, ব্রেন, ফুসফুস ও শ্বাসনালীর দিকে। তাই, ‘আমরা বাঁচার জন্য খাই’ উক্তিটি টিকে রয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে উক্তিটিও বদলে যাবে। শুরু হবে, ‘আমরা মরার জন্য খাই।’ বাঙালি যখন বুঝতে পারবে, আমরা মরার জন্য খাই তখন কারো পরামর্শে নয়, নিজে নিজেই খাওয়া কমিয়ে দেবে।
লেখক : আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

















