শৈল্পিক প্রতীকের মাধ্যমে বাইরের জগতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব
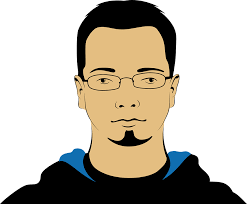
- আপডেট টাইম : বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই, ২০১৯

দুলাল আল মনসুর:
রাশিয়ার সিম্বলিস্ট কবি, প্রবন্ধকার এবং ঔপন্যাসিক আঁদ্রেই বেলির পুরো নাম বরিস নিকোলায়েভিচ বুগায়েফ। তার মাস্টারপিস উপন্যাস ‘পিটার্সবার্গ’। এ উপন্যাসে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কথা বলা হয়েছে। ভাষার ব্যবহার এবং নিরীক্ষাধর্মিতার কারণে জয়েসের ‘ইউলিসিস’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয় এ উপন্যাসটিকে। ভøাদিমির নবোকভ এ উপন্যাসটিকে বিশ শতকের চারটি সেরা উপন্যাসের অন্যতম বলে মনে করেন। প্রবন্ধকার ইসাইয়া বার্লিন বলেন, আঁদ্রেই বেলি ‘অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীজাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী, তবে রাশিয়ার প্রচলিত গোঁড়ামির দৃষ্টিতে তিনি বোকা।’
খুব অল্পবয়সে তার জার্মান সঙ্গীতের প্রতি টান তৈরি হয়। লেখালেখি শুরুর আগে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এ ছাড়া তার আগ্রহের বিষয় ছিল রোমান্টিক সঙ্গীত, ধর্মবিষয়ক পড়াশোনা, সুফিবাদ; সপেনহাওয়ান, নিটশে কান্ট প্রমুখের প্রতি ছিল জানার আগ্রহ। মা ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তিনি সন্ধ্যায় ছেলেকে চোপিন এবং বিটোফেন বাজিয়ে শোনাতেন, ছেলেকে কনসার্টেও নিয়ে যেতেন। পরবর্তী সময়ে তার লেখায় ধ্বনির একটা বিশেষ জায়গা তৈরি হয়।
শতাব্দীর শুরুতে সিম্বলিস্টদের দ্বিতীয় প্রজন্মের সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী লেখক ছিলেন বেলি। তাদের সময়টাকে ‘রুপালি যুগ’ বলা হয়। শিল্পের মধ্যে আত্মিক এবং মরমি উপাদানের উপস্থিতির ওপর জোর দেন সিম্বলিস্টরা। শৈল্পিক প্রতীকের মাধ্যমে বাইরের জগতের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন বেলি। তার কৈশোরেই বেলি বহুবার ভøাদিমির সোলোভিওভের সাহিত্য আড্ডায় হাজির হয়েছেন। সোলোভিওভ মনে করতেন, কবিতার প্রতীক হলো মহাকালে প্রবেশের দরজা। তার ‘শব্দের যাদু’ প্রবন্ধে বেলি জানান, শব্দ হলো নতুন জগৎ তৈরির জাদুকরী শক্তি। তিনি বলেন, “যখন আমি ‘আমি’ শব্দটা উচ্চারণ করি, তখন আমি একটা ধ্বনির প্রতীক সৃষ্টি করি। অস্তিত্ব আছে এমন একটা কিছুর প্রতীক তৈরি করি আমি। শুধু ওই মুহূর্তটাতেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। চিত্রকল্পের প্রতীক রূপকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শব্দ থেকে জন্ম হয়েছে পুরাণের; পুরাণ থেকে ধর্মের; ধর্ম থেকে দর্শনের এবং দর্শন থেকে জন্ম হয়েছে শব্দের।” বেলি মনে করেন, ‘শব্দের একটা যৌক্তিক অর্থ আছে; আর যেকোনো ধ্বনি-প্রতীকের আছে একটা আবেগী অর্থ।’
বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের সময় বেলি প্রচ- দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন। তবু জার শাসনের পতনকে তিনি স্বাগত জানান। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কো ও পেট্রোগ্রাডে ছিলেন। ১৯২১ সালে ব্লকের মৃত্যুর পর বেলি বার্লিন চলে যান এবং সেখানে কয়েক বছর কাটান। ক্যাফে ল্যান্ডগ্রাফে অন্যান্য কবি-লেখকের সঙ্গে তার আড্ডা হয়। তখন ক্যাফে ল্যান্ডগ্রাফকে বলা হতো ‘শিল্পবাড়ি’। আঁদ্রেই বেলি, সেরগেই এসেনিন, বরিস পাস্তারনাক, মারিনা সুয়েতায়েবা প্রমুখ কবি-লেখকের নিয়মিত আনাগোনা ছিল সেখানে। তারা নিজেদের লেখা পড়ে কিংবা আবৃত্তি করে শোনাতেন উপস্থিত অন্যদের। বেলির স্ত্রীর সঙ্গে তত দিনে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিরহী বেলি সুয়েতায়েবার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। সুয়েতায়েবার মেয়ের বর্ণনায়, ‘বেলির চাহনি ছিল বিড়ালের চাহনির মতো ক্যাপাটে।’ বেলি ১৯৩৪ সালের ৮ জানুয়ারি মারা যান। মৃত্যুর বছরখানেক পরে রাশিয়ার ভাষাবিদ এবং সাহিত্যিক তাত্ত্বিক রোমান জ্যাকবসন মতামত দেন, বেলি, মায়াকোভস্কি, পাস্তারনাক এবং আরো কয়েকজনের গদ্য রাশিয়ার গদ্যের পুনর্জাগরণের একটা গুপ্ত পথের সন্ধান দিচ্ছে।













