আমিও একদিন ছিলাম তোমাদের মতো
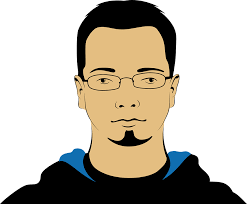
- আপডেট টাইম : শনিবার, ১ জুন, ২০১৯

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন জোটের মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম সম্প্রতি বলেছেন, ‘এই দেশে আপনি দেখবেন পয়সা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেনা যায়, পয়সা দিয়ে এমনকি আইনজীবী কেনা যায়, এমনকি অনেক আদালত কেনা যায় পয়সা দিয়ে এ দেশে’ [বাংলানিউজ২৪.কম, ১৫/৫/২০১৯]। ছোট করে হলেও দেশের অনেক সংবাদমাধ্যমেই এই খবর ছাপা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত শিরোনামে খবরটি ছাপা হলেও এটা বিশাল তাৎপর্য বহন করছে।
এই খবর পড়ে মনে হলো- একদিন আমিও তো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দলে, যাদের ‘আমলা’ বলা হয়, তাদের দলে ছিলাম। এমন বক্তব্য আমাকে সত্যিকার অর্থেই চিন্তিত ও আতঙ্কিত করে তুলেছে। উক্তিটি যিনি করেছেন তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। কেন উনি এ কথা বলেছেন, কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, জানা নেই। হতে পারে অনেকসময় প্রেক্ষাপটের বাইরে গিয়ে মুখ ফসকে এমন কথা বেরিয়ে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু বিষয়টা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। এই আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য কারা? সেই আইন আদালতের বিচারকই বা কারা? আমাদের আদালতে যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন, তারা কারা? তারা তো আমাদেরই সন্তান বা ঘনিষ্ঠজন। আমার এই বয়সে হয়তো বলতে পারি, তারা আমার ছেলেমেয়ে অথবা নাতি-নাতনীর সমান। যা হোক, এ ধরনের বক্তব্য আমার কাছে নিতান্তই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কারণ একদিন আমিও তো তাদের মতো ছিলাম।
১৯৬৩ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (ইপিসিএস) যোগ দিয়েছিলাম। পরে সিএসএস (সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস) পরীক্ষা দিয়ে ইসলামাবাদ চলে যাই। ইপিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগদান করার পর আমাকে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম পোস্টিং দেয়া হলো চট্টগ্রামে। পরে বদলি হয়ে ময়মনসিংহে চলে যাই। বলতে গেলে, ময়মনসিংহেই প্রথম আমার আইন-আদালত ও বিচার-আচার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ। তখন অনেক ঘটনার মধ্যে প্রধানত তিনটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। প্রথম ঘটনা ছিল বিচার কাজ সংক্রান্ত। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শ্বশুর উমেদ আলী সাহেব তখন ময়মনসিংহ আদালতে প্র্যাকটিস করতেন। আমার কাছে একটি মামলা আসে। এর আসামি হচ্ছেন এক বৃদ্ধ চাচা, আর বাদি হচ্ছেন তার ভাতিজারা।
আসামির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা ছিল, তা দেখে আমার মনে হচ্ছিল, চাচার সাজা হতে যাচ্ছে। কিন্তু চাচাকে দেখার পর আমার মনে হলো, আর যাই হোক এ লোক চুরি করতে পারে না। এজলাসে সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ করে চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ভাতিজারা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তিনি বললেন যে, তার কোনো সন্তান নেই। মামলাকারীরা তার বাগানে ঢুকে আম-কাঁঠাল সব পেড়ে নিয়ে যায়, নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়। এ নিয়ে তাদের বকাবকি করেছি, তাদের মা-বাবার কাছে নালিশ করেছি। তাই তারা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পরে ভাতিজাদের ডেকে কথা বলি, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। তারা মামলা তুলে নিতে রাজি হয়। প্রথাগত নিয়মের বাইরে গিয়ে প্রচুর মামলা নিষ্পত্তি করেছি।
দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো : একদিন আমি অফিসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম, এক প্রকৌশলীকে এলাকার ছেলেরা মারধর করেছে, তার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে। আমাকে ঘটনা তদন্তের ভার দেয়া হয়। ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে যা জানতে পারলাম, তা স্তম্ভিত করে দেয়ার মতো। ওই প্রকৌশলীর বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি অনেক কষ্ট করে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর ছেলে আর মা-বাবার সাথে যোগাযোগ রাখেন না বা তাদের দেখাশোনা করেন না। ঘটনার দিন বাবা গ্রামেরবাড়ি থেকে এক টিন মুড়ি নিয়ে ছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে সে সময় তার বন্ধুদের সাথে বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন।
বাবার ভালো পোশাক ছিল না। ছেলের বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, উনি কে? বাবার সামনে ছেলে বলেছে, আমার বাসার কামলা। এটা শুনে বাবা খুবই মনঃক্ষুণœ হন। তিনি সবার সামনে ছেলেকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আমি কে, তা তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস’। এরপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তখন গুজব ছিল ভারতের টিকটিকিরা (গোয়েন্দা) বিভিন্ন স্থানে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এলাকার কিছু অতি উৎসাহী ছেলে বৃদ্ধ লোকটিকে টিকটিকি মনে করে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। বাবা সব কিছু খুলে বললে উত্তেজিত ছেলেরা বাড়ি থেকে ধরে এনে ওই ইঞ্জিনিয়ারকে মারধর করে এবং তার বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। আমি বিষয়টি তদন্ত করে রিপোর্ট দিলাম।
আর তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, আমাকে ময়মনসিংহের একটি খাদ্যগুদাম পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আমার কাজটি ছিল গুদামে যত খাদ্যশস্য জমা করা হতো, তার পাঁচ শতাংশ পরীক্ষা করে এ মর্মে রিপোর্ট দেয়া যে, জমা করা শস্যের পরিমাণ সঠিক রয়েছে। এর মান সম্পর্কেও রিপোর্ট দিতে হতো। পরিদর্শনে গিয়ে দেখি, সেখানকার ফুড ইন্সপেক্টর হচ্ছেন আমার এক কলেজমেট। সে আমাকে পেয়ে বেশ খাতির যতœ করতে থাকে। এভাবে তার সাথে ঘুরেফিরে দুই-তিন দিন কেটে গেল। যখন তাড়া দিলাম তখন সে আমাকে বলল, ‘মাপজোখ করার দরকার কী? ঠিকঠাক মতো মাপতে গেলে মাসখানেক লাগবে। তার চেয়ে তোমাকে হাজার দশেক টাকা দিচ্ছি।’ সে সময় ১০ হাজার টাকায় ৮-১০ কাঠা জমি কেনা যেত। বললাম কেন? আমি তো তোমার কোনো কাজ করে দিইনি। সে বলল, ‘পাঁচ শতাংশ শস্য পরীক্ষা করা হয়েছে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে’ বলে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। সে আরো জানায়, এসব থেকে মোটামুটি লাখ খানেক টাকা আসবে। বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিতে হবে। সেখান থেকেই আমাকে ১০ হাজার টাকা দেয়া হবে।
চাকরিজীবনে আমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রথম। আমাকে যে সময় দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র এক শতাংশের মতো মাপতে পারলাম। এত কম সময়ের মধ্যে এত বিপুল শস্য মাপা সম্ভব নয়, উল্লেখ করে খাদ্য বিভাগের নিয়ন্ত্রক বরাবর চিঠি দিলাম। আমাকে প্রশংসা করে উত্তর এলো, আমার আগে কেউ সময় স্বল্পতার কথা উল্লেখ করে রিপোর্ট দেননি। এরপর কী হয়েছিল, আর জানি না। বিচারক হিসেবে বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পাইনি। তবে আমার মনে হয়েছে, নিয়মের ভেতরে থেকে সব সময় ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। ন্যায়বিচার করতে হলে কখনো কখনো নিয়মের বাইরে যাওয়াটাও জরুরি। আইন গণিতশাস্ত্র নয়, তাই ধরাবাঁধা সূত্র মেনে চলে না। সেখানে ক্ষেত্রমতো বাঁকা করার সুযোগ থাকাও দরকার। যাক, আমার সিএসএস পরীক্ষার রেজাল্ট হলো, পরীক্ষায় পাস করলাম। পোস্টিং হলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ে। পদ ছিল অ্যাসিসট্যান্ট ফাইন্যান্স এডভাইজার। চলে গেলাম সেখানে।
সেখানে গিয়ে দু’টি বিষয় বুঝেছিলাম। একটি হলো সাধারণ পাকিস্তানিরা মানুষ হিসেবে ততটা খারাপ নয়, যতটা ভেবেছিলাম। আর দ্বিতীয়টি, অফিসারদের মধ্যে ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়ার মতো উদারতা ছিল। সে সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ে পূর্ব পাকিস্তানি ছিলেন হাতেগোনা। কেন্দ্রীয় সরকারের আট শতাংশও পূর্ব পাকিস্তানি ছিলেন না। অফিসার পর্যায়ে আরো কম। অথচ পূর্ব পাকিস্তানিরাই আন্দোলন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠন করেছিলেন। অ্যাসিসট্যান্ট ফাইনান্স এডভাইজার হিসেবে তথ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত ছিলাম। তখন আয়ুব খানের আমল। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন সুপরিচিত আলতাফ গওহর।
অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাইন্যান্স এডভাইজার হিসেবে কাজ করার সময় বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। আমার মাথার মধ্যে সব সময় ঘুরপাক খেতো- পশ্চিম পাকিস্তানে যখন কাজ করার সুযোগ হয়েছে, তখন পূর্ব পাকিস্তান যেসব বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সেগুলো যতটা সম্ভব পেশাগত প্রটোকলের মধ্যে থেকে তুলে ধরা এবং সম্ভব হলে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কিছু করা। হাফিজ জলন্ধরী ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের জাতীয়সঙ্গীত ‘পাক সার জমিন শাদ বাদ…’ রচনা করেন। তাকে প্রতিবার গান সম্প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে দুই টাকা রয়্যালটি দেয়া হতো। এই রেওয়াজ অনেক দিন ধরে ছিল। তবে প্রতি বছর এর অনুমোদন দিতে হতো।
অর্থ মন্ত্রণালয়ে থাকার কারণে রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে ফাইলটি আমার কাছে আসে। ফাইল অনুমোদন করার আগে ভাবলাম, আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কত রয়্যালটি দেয়া হয় তা জানা দরকার। কিন্তু শুধু নজরুলের কথা জানতে চাওয়া ‘অন্য রকম’ মনে হতে পারে ভেবে কৌশলে কবি আল্লামা ইকবাল (যাকে ‘পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা’ বলা হয়), রবীন্দ্রনাথ, উম্মে কুলসুম কে কত রয়্যালটি পাচ্ছেন তা জানতে চেয়ে ফাইলটি ফেরত পাঠাই। কয়েক দিনের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে রয়্যালটির একটি চার্ট দেয়া হলো। দেখি ইকবাল প্রতি গানের জন্য বার আনা, নজরুল ছয় আনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চার আনা, বিখ্যাত মিসরীয় শিল্পী উম্মে কুলসুম আট আনা পাচ্ছেন। এরপর তুলনামূলক আলোচনায় উল্লেখ করি, আল্লামা ইকবালের রয়্যালটি ন্যায্য মনে হচ্ছে না। আর কাজী নজরুল ইসলামকে অন্তত এক টাকা রয়্যালটি দেয়া উচিত। একই সাথে প্রস্তাব পাঠাই অন্যদের তুলনায় হাফিজ জলন্ধরীকে দুই টাকা রয়্যালটি দেয়া অন্যায্য বরং তাকে এক টাকা দেয়া যেতে পারে। ফাইলে নোট লিখে ওপরে পাঠিয়ে দিলাম।
ডেপুটি ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার ছিলেন একজন পাঞ্জাবি। তিনি ফাইল পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি হাফিজ জলন্ধরীকে চিনি কি না। বললাম, চিনি না। জানালেন, তিনি প্রেসিডেন্টের বন্ধু। আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট। ডেপুটি ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার আমাকে নোট পরিবর্তন করতে বললেন। তবে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করি। আমি বলেছি, স্যার, আপনি ভিন্নমত পোষণ করে নোট দিলে সমস্যা থাকে না। তিনি এতে বিরক্ত বোধ করে নোট না লিখে শুধু সই করে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনিও শুধু সই করে ফাইলটা সেক্রেটারি গোলাম ইসহাক খানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পরে ফাইল যায় তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের কাছে। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। তাদের মধ্যে এতটাই ঘনিষ্ঠতা ছিল যে গওহরকে বলা হতো, পাকিস্তানের ডি-ফ্যাক্টো ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি ফাইল পেয়ে আমার ওপর খুব ক্ষেপে গিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। প্রেসিডেন্ট ফাইলের ওপর নোট দেন, ‘on humanitarian ground, the royalty may be renewed.’ এ কথা বলার মানে আমার নোট ঠিক ছিল। পরে ফাইল আমার কাছে ফেরত এলে প্রেসিডেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী জিও (সরকারি আদেশ) ইস্যু করি। এ বিষয়গুলো আমি জানতে পারছিলাম। কারণ, ফাইলটি কখন কোথায় যাচ্ছে তার ওপর নজর রাখছিলাম। পরে আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে এ জন্য প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি।
এটা বলছি এ কারণে যে, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিনি, নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকতে শিখেছি। সম্মানের সাথে ঊর্ধ্বতনদের ‘না’ বলতে শিখেছি। নেগেটিভ বিষয়কে পজিটিভলি দেখতে শিখেছিলাম।
তাই যখন বর্তমান সময়ের তরুণদের দিকে তাকাই, তখন ভাবি এরা কেন অন্য রকম হবে। তখন তো পুলিশ বাহিনীতে কোনো মেয়ে ছিল না। আমার সময়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে একটি মেয়ে ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলে। আমার মতো একই অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে। আমাকে খুব ¯েœহ করতেন। আর এখন সরকারের বিভিন্ন সার্ভিসে কত মেয়ে কাজ করছেন। কত তরুণ কাজ করছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ শুনি, তখন আমার খুব দুঃখ হয়। তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, তোমরা বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করো কী করতে হবে; নিষ্ঠাবান হও, দেশপ্রেম শেখো। তোমরা তো কোনো ব্যক্তি বা দলের চাকর নও।
আরেকটি ঘটনার কথা বলি। তখন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে আমার শেষ পোস্টিং ছিল ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে। তখনো এলাকাটি বেশ ‘বিপজ্জনক’ বলে কুখ্যাতি ছিল। নির্বাচনী দায়িত্ব দিয়ে ডিসি আমাকে সেখানে পাঠান। আইয়ুব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। নির্দেশ ছিল অনেকটা যেন, আয়ুব খানের মুসলিম লীগকে আনুকূল্য দেখাই। আমি ভাবলাম, ডিসির তা বলা ঠিক আছে। কিন্তু আমি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করব। নির্বাচনের বিভিন্ন কাজে যখন দুই পক্ষ আমার কাছে আসে, আমি তাদের সমান সুযোগ দিই। এ কথা সততার সাথে বলছি। আমার বিবেক বলেছে- আমি রাষ্ট্রের পয়সা নিচ্ছি, কোনো ব্যক্তির নয়। এসব কথা বলার অর্থ হলো- আজ যারা সরকারি চাকুরে, তাদের বলা- ‘তোমরা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করো। জীবনকে বড় করে দেখার চেষ্টা করো। জীবনের লক্ষ্যকে বড় করে দেখো। এই সোনার বাংলার মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। এসব মানুষের পয়সাতেই তোমরা লেখাপড়া করেছো।’
অনেক জায়গায় বলেছি যে, বাংলাদেশে যে কর ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে ৮৮ শতাংশ করই পরোক্ষ, যা গরিব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। আর প্রত্যক্ষ কর বড় জোর ১০ শতাংশ। এটা ধনীরা দেয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু কর ব্যবস্থায় নানা রকম ফাঁকফোকর থাকে। তাতে ধনীরা ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পায়। তাই বলতে গেলে, গরিবের পয়সাতেই দেশ চলে। যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তারা তো গরিবের পয়সাতেই পড়ছে। তাই গরিবদের কাছে ওই সব শিক্ষার্থী দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতার খাতিরে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আমার জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে দেশের মানুষের কিছুটা উপকার করার চেষ্টা করছি। এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই, বরং বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতেই এসব কথা বলছি।
লেখক : প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি:, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা



















